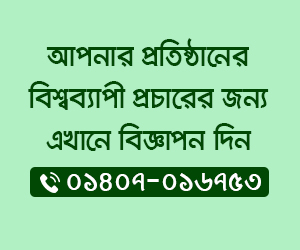চাকরি অধ্যাদেশ বাতিলে সচিবালয়ে বিক্ষোভ

সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে ‘সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’কে ঘিরে। গত বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন দেওয়ার পর থেকেই সচিবালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মচারীরা ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে আসছেন। টানা তৃতীয় দিনের মতো সচিবালয়ে বিক্ষোভ, মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি চলছে। অনেকে এই অধ্যাদেশকে ‘নিবর্তনমূলক’ ও ‘কালাকানুন’ বলে উল্লেখ করছেন।
প্রশ্ন উঠেছে, কী এমন আছে এই নতুন আইন সংশোধনীতে, যা এত আলোচনার জন্ম দিয়েছে? কেন সরকারের নিজস্ব কর্মচারীরাই এর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন?
অধ্যাদেশ অনুযায়ী, ২০১৮ সালের সরকারি চাকরি আইন (৫৭ নং আইন)-এ একটি নতুন ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে—ধারা ৩৭ক। এই ধারায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য শৃঙ্খলাবিধি ও দণ্ড সংক্রান্ত একটি বিশেষ বিধান যুক্ত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যদি কোনো সরকারি কর্মচারী অনানুগত্যমূলক আচরণ করেন, শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন, যৌথভাবে কর্মবিরতিতে যান, কাজ থেকে অনুপস্থিত থাকেন, অন্যদের উসকানি দেন বা কাজ করতে বাধা দেন—তবে তাকে ‘অসদাচরণকারী’ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
এই অসদাচরণের জন্য কর্মচারীর বিরুদ্ধে কয়েকটি কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: চাকরি থেকে অপসারণ, বরখাস্ত করা, বা নিম্নপদে অবনমিত করে দেওয়া। আর এসব শাস্তি কার্যকর করতে কোনো আদালতের রায় বা স্বাধীন তদন্তের প্রয়োজন নেই; নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা তার মনোনীত ব্যক্তি অভিযোগ গঠন করে স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তা সম্পন্ন করতে পারবেন।
অভিযুক্ত কর্মচারীকে অভিযোগের ভিত্তিতে সাত কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হবে। যদি তিনি লিখিতভাবে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে সন্তোষজনক জবাব না দেন, তাহলে কর্তৃপক্ষ তার ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে। আবার একই ব্যক্তি শাস্তি আরোপের পর আরও একবার কারণ দর্শানোর সুযোগ দেবেন, এবং সেই জবাব বিবেচনায় নিয়ে চূড়ান্তভাবে দণ্ড আরোপ করা হবে।
নোটিশ জারির ক্ষেত্রেও অধ্যাদেশটি কঠোর। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো না গেলেও, তার বাসার বাইরে টাঙানো, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বা ই-মেইলে পাঠালেই সেটি ‘জারি হয়েছে’ বলে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ, নোটিশ প্রাপ্তির বাস্তব প্রমাণের প্রয়োজন থাকছে না।
আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, এই অধ্যাদেশে আপিল প্রক্রিয়াও সীমিত করা হয়েছে। সাধারণ ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে আপিল করতে পারবেন। তবে যদি শাস্তিটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে আর কোনো আপিল করার সুযোগ নেই—শুধু পুনর্বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করা যাবে, যার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এর মানে হচ্ছে, রাষ্ট্রপতির আদেশের বিরুদ্ধে দেশের কোনো ফোরামে আর চ্যালেঞ্জ করার পথ থাকছে না।
সরকারি কর্মচারীদের অভিযোগ, এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে তাদের মৌলিক অধিকার, বিশেষ করে মতপ্রকাশ, সংগঠিত হয়ে দাবি আদায় এবং যৌক্তিক বিরতি গ্রহণের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। এই আইন ব্যবহার করে সহজেই অসন্তুষ্ট বা সমালোচনামূলক অবস্থান নেওয়া কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পথ সুগম হয়ে গেল। একজন কর্মচারী যদি তার অধিকার নিয়ে কথা বলেন, কিংবা কর্মবিরতির ডাক দেন, তাকে ‘অনানুগত্যের’ দায়ে চাকরি হারাতে হতে পারে।
এই অবস্থায় কর্মচারীরা মনে করছেন, নতুন এই আইন সরকারি চাকরিকে একটি বন্দিত্বমূলক কাঠামোয় পরিণত করছে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে মতপ্রকাশ ও প্রশ্ন তোলার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অনেকেই এটিকে ক্ষমতাকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখছেন, যেখানে আমলাতন্ত্রকে ভয় ও শাস্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে।
বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা এই অধ্যাদেশের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, এ ধরনের অধ্যাদেশ আইনত অগ্রহণযোগ্য এবং এটি বাতিল না করা হলে দেশের প্রশাসনব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি সংকট সৃষ্টি হবে। সরকার এখন এক অস্বস্তিকর অবস্থানে রয়েছে—প্রশাসনের স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত সচিবালয়ের কর্মচারীরা যদি আন্দোলন চালিয়ে যান, তাহলে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে বড় ধরনের অচলাবস্থা তৈরি হতে পারে।
এই অধ্যাদেশ নিয়ে সমালোচনা শুধু কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রশাসনবিষয়ক বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে রাষ্ট্র যদি অধীনস্থদের ন্যায্য অধিকার হরণ করে, তাহলে তা দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর নয়—বরং এটি আরও বড় অসন্তোষ ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার জন্ম দিতে পারে।